উচ্চমাধ্যমিক বাংলা প্রশ্নোত্তর
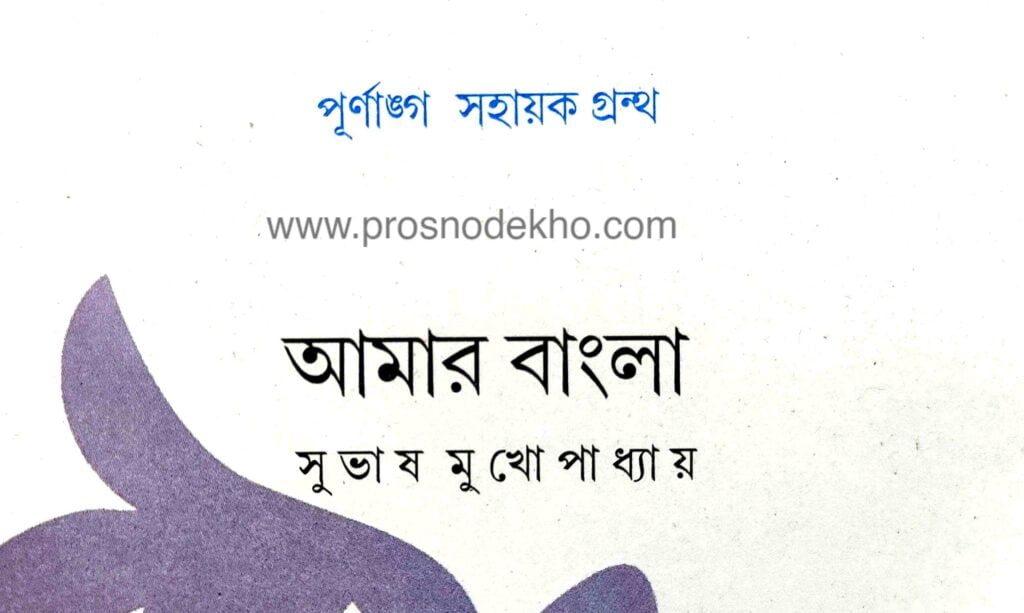
আমার বাংলা – সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের – উচ্চমাধ্যমিক বাংলা বড় প্রশ্ন (Essay Type) উত্তর | WBCHSE HS Bengali Solved Question Answer
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচিত আমার বাংলা পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ থেকে (গারো পাহাড়ের নীচে, ছাতির বদলে হাতি, কলের কলকাতা, মেঘের গায়ে জেলখানা ও হাত বাড়াও) রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তরগুলি (Descriptive Question and Answer) আগামী পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক বাংলা পরীক্ষার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে MCQ, SAQ প্রশ্ন থাকে না।
আমার বাংলা – সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের – উচ্চমাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা প্রশ্ন ও উত্তর | WBCHSE HS Bengali Question and Answer
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (Essay Type) | আমার বাংলা – সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের – উচ্চমাধ্যমিক বাংলা প্রশ্ন ও উত্তর | WBCHSE HS Bengali Question and Answer

গারো পাহাড়ের নীচে
১. “কিন্তু হাতি-বেগার আর চলল না।”– হাতি-বেগার আইন কী ? তা আর চলল না কেন ? (২০১৬)
উত্তরঃ
‘হাতি-বেগার আইন’: সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের আমার বাংলা গ্রন্থের ‘গারাে পাহাড়ের নীচে’ রচনায় আমরা হাতি-বেগার আইনের বর্ণনা পায়। উনিশ শতকের শেষদিকে গারাে পাহাড়ে এই জমিদারি আইন চালু ছিল। পাহাড়ের ওপর মাচা বেঁধে সেখানে সশস্ত্র জমিদার সেপাইসান্ত্রি-সহ বসে থাকতেন হাতি শিকারের উদ্দেশ্যে। গ্রামের ছেলে বুড়াে-সহ প্রতিটি পুরুষপ্রজাকে নিজেদের খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে হাতি-বেড় দেওয়ার জন্য আসতে হত। যে জঙ্গলে হাতি আছে, সেই জঙ্গলটা তাদের সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ঘিরে ফেলতে হত। জমিদারের যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয় তার ঢালাও ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু প্রজারা কিছুই পেত না। এমনকি এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সাপের কামড়ে বা বাঘের মুখে তাদের অনেকেরই মৃত্যু হত।
হাতি-বেগার আইন না চলার কারণ : জমিদারের হাতি শিকারের শখ মেটানাের উদ্দেশ্যে তৈরি এই আইন গারাে পাহাড়িরা বেশিদিন সহ্য করেনি। এর বিরুদ্ধে তারা গােরাচাদ মাস্টারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। গারাে পাহাড়সংলগ্ন প্রতিটি চাকলায় ক্রমে ক্রমে মিটিং শুরু হয়। প্রতিটি কামারশালায় তৈরি হতে থাকে অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু এতসব প্রস্তুতি সত্ত্বেও জমিদারের সৈন্যদলের কাছে বিদ্রোহী প্রজারা পরাজিত হয়। কিন্তু বিদ্রোহ দমনে সফল হলেও জমিদারেরা আর হাতি-বেগার আইন চালু রাখতে সাহস পেলেন না। এভাবেই গারাে পাহাড়ে হাতি-বেগার প্রথা লুপ্ত হয়।
২. “তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল”— প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল কেন ? সেই বিদ্রোহের ফল কী হয়েছিল ?
উত্তরঃ
“পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে,
হুজুর জেনে রাখুন।
খাজনা এবার মাফ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন ”
এমন বিধ্বংসী, এমন প্রতিবাদী, এমন শ্রমজীবীর কণ্ঠ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন কবি সুভাষ মুখােপাধ্যায়। সাম্যে বিশ্বাসী সমাজ বদলের স্বপ্নে উন্মুখর, বিদ্রোহের অগ্নিকোণেও তিনি ফুটিয়ে তােলেন নবযুগের ফুল। তাই সামন্ত নিষ্ঠুরতায় বিপন্ন, ইংরেজ কুশাসনের কবলে বন্দি বাংলাদেশেও তিনি সাধারণের সম্মিলিত জয়ের ছবি ফুটে উঠতে দেখেন।
নিষ্ঠুর জমিদারতন্ত্রের পরিচয়: গারাে পাহাড়ের আদিবাসীরা প্রকৃতির সব বিরুদ্ধতা অতিক্রম করে, পাথরের বুকের ওপর ফসলের সমারােহে আনে সবুজ বিপ্লব। তারপর সেই ফসল যখন পাকে, তখনই মৃত্যুদূতের মতাে উপস্থিত হয় জমিদারের পাইক, বরকন্দাজরা। তাদের খাজনা আদায়ের ভয়ংকর থাবা এসে সবই কেড়ে নিয়ে যায়। জমিদারের ‘ টঙ্ক ‘ দিতে গিয়ে চাষিদের জীবন সমীকরণের অঙ্ক শূন্য হয়ে যায়।
হাতি-বেগার প্রথাঃ গারাে পাহাড়তলি অঞ্চলে এক বিশেষ জমিদারি আইন ছিল। নাম হাতিবেগার। জমিদারি খেয়াল ও বর্বরতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন এই প্রথা। জমিদারের শখ ছিল হাতি ধরার। তার জন্য আড়ম্বরে মাঁচা বাঁধা হতাে। সেখানে সেপাই নিয়ে আসন অলংকৃত করবেন মহামান্য মহাবীর জমিদার। একান্ত নিরিবিলিতে সব শৌখিনতা বজায় রেখেই। তাই পান থেকে চুন না খসার ঢালাও ব্যবস্থা করা হতাে। এবং যে অঞ্চলে হাতি আছে, সেই জঙ্গলকে ঘিরে বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে ছেলে – বুড়াে সমস্ত প্রজাকে। প্রত্যেক গ্রাম থেকে তাই আসতে হতাে খাদ্য নিয়ে। যারা হাতি বেড় দিত, তাদের অনেকেই সাপের কামড়ে বা বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ দিতে বাধ্য থাকতাে। তাতে কী হলাে ! মহামান্য জমিদারের হাতি ধরার মহাবীরত্ব তাে প্রকাশ পেল ! হাতির জন্য প্রজাদের এই যে বেগার শ্ৰমদান, এমনকি বে – সহায় প্রাণদান করার প্রথাই হলাে ‘ হাতিবেগার প্রথা ‘।
হাতি-বেগার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহঃ হাতিবেগার এমন চরম অত্যাচারের আগুন হয়ে প্রজাদের জীবন পুড়িয়ে দিলাে যে, চিরকালের মৌন – শান্ত – সর্বসহপ্রজারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠলাে। আর প্রতিটি বিদ্রোহের পিছনেই থাকে একজন মানবতাবাদীর নির্ভীক মুখ ; এখানে সেই বিদ্রোহের জলন্ত মুখ হয়ে ওঠে গােরাচাঁদ মাস্টার। তিনি চাকলায় চাকলায় মিটিং এ বসিয়ে প্রজাদের সচেতন করলেন। বােঝালেন, অন্যায়কে মেনে নেওয়া সবচেয়ে বড়াে অন্যায়। ফুঁসে উঠলাে মানুষ। কামার ঘরে তৈরি হতে লাগল অস্ত্রশস্ত্র। সমবেত প্রজারা হলাে সজ্জাবদ্ধ। তারা গর্জে উঠলাে ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়েই। কিন্তু জমিদারের নৃশংস দমননীতিতে এবং আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়ােগে প্রজাদের হার হলাে। তবু হারের পরেও এল জিত -হাতিবেগার বন্ধ হলাে। সেই থেকে চৈতন্যনগরে, হিন্দুলকোনায় প্রচলিত হলাে বিদ্রোহের সেই গল্প। রচিত হলো কিংবদন্তি। বিদ্রোহীদের উত্তর পুরুষরা তা বহন করে চলল যুগ যুগান্তর ধরে।
৩. ‘গারাে পাহাড়ের নীচে’ রচনা অবলম্বনে সুসং পরগনার নিসর্গ প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির বর্ণনা দাও।
উত্তরঃ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুভাষ মুখােপাধ্যায় ‘ গারাে পাহাড়ের নীচে ’ গদ্যাংশে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।
গারাে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত সুসং পরগনার ভালােলাগা অনুভূতি লেখকের ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে। গাড়ি চলাচলের রাস্তা এতই অমসৃণ যে, চলার পথে কান্না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই ওই পাহাড়ি পথে হেঁটে যাওয়াই আরামদায়ক। সুসং পরগনার অন্যতম আকর্ষণ সােমেশ্বরী নদী। এই নদীকে শীতের সময় দেখে শান্তশিষ্ট মনে হয়। স্নিগ্ধ জলরাশি দেখে হেঁটে পার হওয়ার বাসনা জাগতে পারে। কিন্তু জলে পা দিলেই মনে হবে কেউ যেন পায়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হবে যেন এ নদীর স্রোত নয়, কুমিরের ভয়ংকর দাঁতের কামড়। এমনটি মনে হতে পারে যে, ভিতরে ভিতরে সোমেশ্বরী যেন ভয়ংকর রেগে আছে।
অবশ্য ফেরি নৌকাতে গােরু – ঘােড়া – মানুষ নিশ্চিন্তে আরামে পার হয়ে যাচ্ছে। ফেরি নৌকার হিন্দুস্থানি মাঝির মেজাজ ভালাে থাকলে শহরের বাবুর কাছে দেশ – বিদেশের খবরাখবর জানতে চাইবে। কিংবা হয়তাে গর্বিত স্বরে দাবি করবে, তার বিহারি মনিব হল বাংলার সব ফেরিঘাটের মালিক। গারাে পাহাড়ের সবুজের স্পন্দনভরা সুসং পরগনা লেখকের সৌন্দর্যপিয়াসী মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তারই প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে আলােচ্য রচনায়।
৪. গারাে পাহাড়ের নীচে যারা বাস করে তাদের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
উত্তরঃ সুভাষ মুখােপাধ্যায় সমাজের পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র মানুষের কথা বলেছেন। ‘গারো পাহাড়ের নীচে’ গদ্যাংশে গারােদের জীবনযাত্রার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা হল—
শিকার বৃত্তিঃ গারাে পাহাড়ের দরিদ্র মানুষেরা অত্যন্ত পরিশ্রমে জীবনযাপন করে। বছরে যখন কাজ থাকে না, তখন তারা শুকনাে ঝােপ-ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই সময় তারা মনের আনন্দে পশু শিকার করে। সুভাষ মুখােপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন— “যেন রাবণের চিতা — জ্বলছে তাে জ্বলছেই।”
কৃষিকর্মঃ পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা অমানুষিক পরিশ্রম করে। এদের অধিকাংশ মানুষ হল হাজং সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের পরিশ্রমে গারাে পাহাড় সবুজবর্ণ ধারণ করে।
শােষণ-বঞ্চনাঃ গারাে পাহাড়ের মানুষদের মনে শান্তি থাকে না। লেখক জানিয়েছেন— “মাঠ থেকে যা তােলে, তার সবটা ঘরে থাকে না।” জমিদারের লােকজন এসে সবকিছু তাদের থেকে কেড়ে নেয়। জমিদারের টাকা মেটাতে গিয়ে চাষিরা ফকির হয়ে যায়।
জমিদারি-আইনঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের উপরে জমিদারের নির্মম শাসনের কথা লিখেছেন। ‘হাতিবেগার ’ আইন অনুসারে হাতি ধরতে গিয়ে অসহায় প্রজাদের অনেকেই প্রাণ দিতে হতাে।
বিদ্রোহঃ গারাে পাহাড়ের প্রজারা গােরাচাঁদ মাস্টারের নেতৃত্বে প্রতিবাদ করে। সেই প্রতিবাদ একসময় বিদ্রোহের রূপ পায়। হাতি-বেগার সেখানে আর চলে না।
৫. “জমিদারকে টঙ্ক দিতে গিয়ে চাষিরা ফকির হয়।”— ‘টঙ্ক’ কী ? জমিদারকে ‘টঙ্ক’ দিতে গিয়ে কারা, কীভাবে ফকির হয় সংক্ষেপে লেখাে।
উত্তরঃ ‘টঙ্ক’ শব্দের অর্থ টাকা। এখানে অবশ্য খাজনা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, টঙ্ক হল খাজনাস্বরূপ জমিদারকে দেওয়া অর্থ।
সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের ‘গারাে পাহাড়ের নীচে’ শীর্ষক রচনা থেকে গৃহীত এই অংশে গারাে পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী প্রজারা জমিদারকে টঙ্ক দিতে গিয়ে ফকির হয়ে যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। ফসলের অসীম প্রাচুর্যতা থাকলেও এই সমস্ত উপজাতির জীবনে সুখ-শান্তি ছিল না।
দুষ্ট শনি যেন তাদের জীবনকে বেষ্টন করে থাকে। মাঠে যতক্ষণ ধান থাকে, ততক্ষণই তাদের আনন্দ। মেয়ে-পুরুষ সবাই এক্ষেত্রে মনের সুখে কাস্তে হাতে মাঠে নামে ধান কাটে এবং পিঠে আঁটি বেঁধে নিয়ে খামারে ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে পাওনাগণ্ডা আদায় করতে হাজির হয় জমিদারের পাইক – বরকন্দাজ। ফলে তাদের ফসলের বেশির ভাগটাই চলে যায় জমিদারের খাতে। চাষিরা গালে হাত দিয়ে দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। তারা বলে–
“লাঠির আগায় পাড়া জুড়ােতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা
খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা।।”
অর্থাৎ তারা যেন জমিদারের রাজস্ব হিসাবের গােলকধাঁধা থেকে বেরােতে পারছে না। গ্রামের আল-বাঁধা রাস্তায় পাইক – বরকন্দাজদের পায়ের নাগরার খটাখট শব্দে ছােটো ছােটো ছেলেরা ভয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকোয়। আর খিটখিটে বৃদ্ধরা অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে। এইভাবেই জমিদারকে খাজনার টাকা দিতে গিয়ে প্রজারা নিঃস্ব হয়ে যায়।
৬. “তাই ওরাও আমাদের পর পর ভাবে।”– কাদের কথা বলা হয়েছে ? কেন তারা আমাদের পর পর ভাবে ?
উত্তরঃ উদ্ধৃত অংশে গারাে পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী মানুষদের কথা বলা হয়েছে।
জাত-পাত-বর্ণের ভেদাভেদ আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে প্রাচীন সময় থেকে। এই ভেদাভেদ এক গােষ্ঠীর মানুষকে অন্য গােষ্ঠীর থেকে পৃথক করে রাখে। অন্য গােষ্ঠীর মানুষ নিজেদের উন্নত মনে করে অন্যদের থেকে; আর সেই গর্বে সে হেলায় উপেক্ষা করে অন্যদের বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথাকে। ফলে আঞ্চলিক নৈকট্য সত্ত্বেও দুটি গােষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধি পায় ব্যবধান।
লেখক সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের মতে বাংলাদেশে বসবাসকারী গারাে পাহাড়ের নীচের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে সমতলে বসবাস করা মানুষদেরও তৈরি হয়েছে দূরত্ব। একই অঞ্চলে বসবাস করেও সমতলের মানুষ কোনােরকম খোঁজ নেয়নি আদিবাসী মানুষদের। জানতে চেষ্টা করেনি তাদের কষ্ট কিংবা অসহায়তাকে। তাই ওরাও আমাদের পর পর ভাবে। পরকে আপন করবার জন্যে যে ঔদার্য থাকা দরকার, তা সমতলের মানুষদের নেই। তারা অধিকাংশই আদিবাসীদের ঠকায়। ফলে তাদের বিশ্বাসযােগ্যতা হারিয়েছে। তাই লেখক একথা বলেছেন।
৭. ‘যেন রাবণের চিতা—জ্বলছে তাে জ্বলছেই।” -রাবণের চিতার মতাে আগুন কারা, কোথায়, কী উদ্দেশ্যে জ্বালিয়েছে? এই আগুন তাদের কীভাবে সাহায্য করে থাকে ?
উত্তরঃ রাবণের চিতার মতাে জ্বালানাে আগুন: লেখক সুভাষ মুখােপাধ্যায় ‘গারাে পাহাড়ের নীচে’ রচনায় জানিয়েছেন যে, প্রতিবছর চৈত্র মাসের রাত্রিবেলায় ময়মনসিংহের উত্তরদিকের আকাশে একরাশ ধোঁয়াটে মেঘ দেখা যায়। আসলে ওটা মেঘ নয়, ওটা হল অবিভক্ত বঙ্গদেশের গারাে পাহাড় (বর্তমানে মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্গত)। ওখানে বাস করে বিভিন্ন আদিবাসী। তাদের চাষের জন্য লাঙল, হাল বা বলদ কিছুই নেই। তা ছাড়া পাহাড়ের ওপর থাকে শুধু গাছ আর পাথর, মাটি থাকে না। অথচ ফসল না ফলালে সারাবছর তারা খাবার পাবে না। তাই ফসল ফলানাের উদ্দেশ্যে পাহাড়বাসীরা প্রতিবছর চৈত্রমাসে পাহাড়ের শুকনাে ঝােপঝাড়ে একদিন আগুন ধরিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে জ্বলতে থাকা সেই দাবানলকেই লেখক রাবণের চিতা বলে উল্লেখ করেছেন।
আগুনের সাহায্যকারী ভূমিকাঃ দাবানলের সময় বনের বাঘ, হরিণ, শুয়াের, অজগর প্রভৃতি জন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে ছুটোছুটি করতে থাকে। তখন পাহাড়িরা জন্তুগুলির, বিশেষত শুয়াের ও হরিণগুলােকে শিকার করে মহানন্দে। আগুন জ্বলতে জ্বলতে কয়েকদিনের মধ্যে গােটা জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে পাহাড়ের গা এবং উপত্যকায় কালাে ছাইয়ের একটি পুরু আস্তরণ পড়ে যায়। সেই ছাইয়ের মধ্যেই ফসলের বীজ ছড়ায় পাহাড়িরা। কয়েকদিনের মধ্যেই গারাে পাহাড়ের পােড়া জমি তামাক, ধান এবং অন্যান্য ফসলে ভরে ওঠে এইভাবেই দাবানল সেখানকার জনজাতিদের সাহায্য করে থাকে।
৮. “পাহাড়ি গারােরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং।”—’হাজং’ কথার অর্থ কী ? হাজংদের জীবনযাত্রার পরিচয় দাও।
উত্তরঃ
হাজং-এর অর্থঃ সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের ‘গারাে পাহাড়ের নীচে’ রচনা থেকে সংগৃহীত উদ্ধৃতিটিতে ‘হাজং’ কথাটি প্রকৃতপক্ষে ‘গারাে’ ভাষার একটি শব্দ; যার অর্থ ‘পােকা’।
হাজংদের জীবনযাত্রাঃ উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের এক উপজাতি হল হাজং। গারাে পাহাড়ের পাদদেশে হাজংদের সাথেই গারাে, কোচ, বানাই, ডালু, মার্গান প্রভৃতি উপজাতির মানুষ বাস করে। প্রত্যেক উপজাতির মানুষের চোখেমুখেই পাহাড়ি ছাপ লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত উপজাতির আলাদা আলাদা মাতৃভাষা থাকলেও হাজং ও ডালুরা অদ্ভুত ধরনের উচ্চারণে বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। ‘ত্’-কে ‘ট্’, ‘ট্’-কে ‘ত্’, ‘ড্’-কে ‘দ্’ এবং ‘দ্’-কে ‘ড্’ উচ্চারণ করে তারা। হাজংদের এমন উচ্চারণ শুনলে যে-কোনাে বাঙালিরই হাসি পাবে। একজন বয়স্ক মানুষ ‘দুধ’-কে ‘ডুড’ এবং ‘তামাক’-কে ‘টামাক’ বলছে শুনলে কার না হাসি পায় ?
গারাে পাহাড়ের ঠিক নীচে রয়েছে সুসং পরগনা, যার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে সােমেশ্বরী নদী। এখানে প্রথম বসতি গড়ে তােলে হাজংরাই। এ অঞ্চলের সংখ্যাগুরু আদিবাসী তারাই, গারােরা নয়। গারাে পাহাড়তলির সুসং পরগনায় এসে হাজংরা প্রথম চাষবাস শুরু করে। কৃষিকার্যে তারা ছিল অত্যন্ত দক্ষ। একারণে পাহাড়তলির পাহাড়ি উপজাতি গারােরা হাজংদের কৃষিকাজের দক্ষতাকে তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছিল ‘চাষের পােকা’।
 ছাতির বদলে হাতি
ছাতির বদলে হাতি
১. “চেংমানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল”- চেংম্যান কে ? তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কারণ লেখো।
অথবা,
“তাতে চেংমানের চোখ কপালে উঠলো”- চেংমান কে ? তার চোখ কপালে ওঠার কারণ কী ? (২০১৭)
উত্তরঃ
চেংমানের পরিচয়ঃ- সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের “ছাতির বদলে হাতি” প্রবন্ধের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো গারো চাষী চেংমান। এই দরিদ্র আদিবাসীটি মনমোহন মহাজনের কৌশল বুঝতে না পেরে প্রায় 36 বিঘে জমি হারিয়েছিল।
চেংমানের বিপদঃ- হালুয়াঘাট বন্দরে মনমোহন বন্ধকী- তেজরতির ব্যবসায়ী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। এ মহাজনের ইঁদুর কলে পরে সর্বস্বান্ত হয়েছিল সরল গারো চাষী চেংমান। প্রায় 25 থেকে 30 বছর আগে হালুয়াঘাট বন্দরে সওদা করতে এসেছিল চেংমান। কিছুক্ষণ পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেয় মহাজন মনমোহনের দোকানের বারান্দায়। কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মহাজন সুকৌশলে কলকাতা থেকে আনা নতুন ছাতাটি মেলে ধরে চেংমানের মাথার উপরে। মহাজনের এরূপ আচরণে স্থম্ভিত হয়ে যায় চেংমান। মহাজন তার মনের অবস্থা বুঝে বলেন- “নগদ পয়সা নাই বা দিলে, যখন তোমার সুবিধে হবে দিয়ে গেলেই হল। ওর জন্য কিছু ভেবোনা।” সরল গারো চাষী মহাজনের কৌশল বুঝতে না পেরে নতুন ছাতা মাথায় দিয়ে মহা ফুর্তিতে বাড়ি চলে যায়।
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কারণ:- প্রত্যেক দিনে চেংমান হালুয়াঘাট বন্দরে সওদা করতে এসে ধারের ছাতির দাম মিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কূটনীতিবিদ মনমোহন মহাজন চেংমানের কথায় কান না তুলে এড়িয়ে যান। মহাজন সুযোগ বুঝে চেংমানকে আশ্বস্ত করে বলেন, সময় মতো দাম মিটিয়ে দেওয়ার। এভাবে দেখতে দেখতে এক বছর কেটে যায় মাথা থেকে ছাতির দামের কথা মুছে যায়। কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন ধরে ফেলে মহাজন বলেন- “কি বাছাধন, বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো, পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাও”- একথা শুনে চেংমানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। মহাজন হিসাব কষে দেখলেন ছাতির দাম চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে হয়েছে হাজার টাকা। যা প্রায় হাতির দামের সমান। যা দেখে চেংমানের চোখ কপালে ওঠে।
২. “আর এক রকমের প্রথা আছে -নানকার প্রথা”- নানকার প্রথা কী ? পরে তাদের অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছিল ?
অথবা,
‘ছাতির বদলে হাতি ‘-পাঠ্যাংশ অবলম্বনে জমিদার’দের অত্যাচারের বর্ণনা যা আছে তা সংক্ষেপে লেখো।
উত্তরঃ
নানকার প্রথাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ছাতির বদলে হাতি’ প্রবন্ধে গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের ওপর মহাজনী অত্যাচার ছাড়াও জমিদারের নানকার প্রথার জুলুমের খন্ডচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। নানকার প্রথার দ্বারা জমিদাররা অকথ্য অত্যাচার চালাত। জমিদারদের এই প্রথায় আবদ্ধ প্রজাদের অবস্থা সাধারণ প্রজাদের চেয়েও দুর্বিষহ ছিল। এই প্রজাদের কোনো জমির মালিকানা ছিল না। এমনকি আম-কাঁঠালের অধিকারটুকুও তারা পেত না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা দিতে হতো প্রজাদের। মহাজন তাদের থেকে একমনে দুই মণ ধান আদায় করতো। জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের ভিন্ন ভিন্ন প্রথার মধ্যে কঠোর প্রথা ছিল নানকার প্রথা। প্রজারা জমিদার’দের খাজনা দিতে না পারলে তহশিলদার তাদের কাছারিতে ধরে আনতো। তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে মালঘরে আটকে রাখত। তারপর নিলামে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে খাজনা আদায় করতো পাওনাদারেরা। এছাড়াও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে চাষীদের সম্পত্তি কেড়ে নিতো।এরূপ অত্যাচারের খন্ড চিত্র লক্ষ করা যায় আলোচ্য প্রবন্ধে।
পরবর্তী অবস্থাঃ এভাবে অত্যাচার সহ্য করার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল প্রজাদের । কিন্তু গারো পাহাড়ের নীচে গড়ে ওঠা লাল নিশান তাদের অধিকারের লড়াই শিখিয়েছিল। তাই নওয়াপাড়া, দুমনাপাড়া , ঘোষপাড়া এবং ভুবনকুড়ার চাষিরা বিদ্রোহে জেগে ওঠে। তাদের জেদের কাছে পরাজয় শিকার করে পুলিশ ও কাছাড়ির জমিদার। এভাবে সাম্যবাদী ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে কমিউনিস্ট আদর্শে মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রজারা নানকার প্রথা বন্ধ করেছিল। ভালো হাল -বলদ এর অভাবে প্রজারা হতাশ না হয়ে মিলিতভবে জমি চাষ করতে শুরু করল। পাথুরে রুক্ষ ও শক্ত মাটিতে চাষ করা কষ্টকর হলেও স্বাধীনতার আনন্দের কাছে তা সামান্য। ধীরে ধীরে তারা সভ্য হয়ে ওঠে। আজকে দারোগা পুলিশ পর্যন্ত তুই তোকারি করে কথা বলার সাহস পায়না তাদের সঙ্গে। বরং চেয়ার ছেড়ে তাদের বসতে দেয়। এভাবেই গারো চাষীরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে শেখে।
৩. “২৫-৩০ বছর আগেকার কথা”– পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেকার কাহিনীটি ‘ছাতির বদলে হাতি’ প্রবন্ধ অনুযায়ী বিবৃত করো।
অথবা,
“বানানো গল্প নয়”- কোন গল্প ? সেই গল্পটির বর্ননা প্রবন্ধ অনুযায়ী লেখো।
উত্তরঃ
ভূমিকাঃ ২৫-৩০ বছর আগেকার কাহিনী বিবৃত করেছেন সমাজ সচেতন প্রাবন্ধিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘আমার বাংলা’ প্রবন্ধের অন্তর্গত ‘ছাতির বদলে হাতি’ রচনায়। উত্তর -পূর্ব ভারতের জনজাতির উপর জমিদার, পাওনাদার, মহাজন ও ব্রিটিশদের অত্যাচার প্রজাদের কীরূপ দুরবস্থা করেছিল তার উল্লেখ আছে। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন -“মনমোহন মহাজন গত হয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু সেই মহাজনের পন্থা আজও টিকে আছে।” অর্থাৎ প্রজাদের উপর অত্যাচার করার প্রথা যারা চালু করেছিলেন তারা মারা গেলেও প্রথাগুলি পূর্ব ভারতে আজও প্রচলিত।
উল্লেখিত গল্প ও কাহিনীঃ চেংমানের উপর মহাজন মনমোহনের অত্যাচারের গল্প আলোচ্য অংশে উলেখ করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে প্রায় 25 থেকে 30 বছর আগে হালুয়াঘাট বন্দরে সওদা করতে এসেছিল চেংমান। কিছুক্ষণ পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেয় মহাজন মনমোহনের দোকানের বারান্দায়। কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মহাজন সুকৌশলে কলকাতা থেকে আনা নতুন ছাতাটি মেলে ধরে চেংমানের মাথার উপরে। মহাজনের এরূপ আচরণে স্থম্ভিত হয়ে যায় চেংমান। মহাজন তার মনের অবস্থা বুঝে বলেন- “নগদ পয়সা নাই বা দিলে, যখন তোমার সুবিধে হবে দিয়ে গেলেই হল। ওর জন্য কিছু ভেবোনা।” সরল গারো চাষী মহাজনের কৌশল বুঝতে না পেরে নতুন ছাতা মাথায় দিয়ে মহা ফুর্তিতে বাড়ি চলে যায়।প্রত্যেক দিনে চেংমান হালুয়াঘাট বন্দরে সওদা করতে এসে ধারের ছাতির দাম মিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কূটনীতিবিদ মনমোহন মহাজন চেংমানের কথায় কান না তুলে এড়িয়ে যান। মহাজন সুযোগ বুঝে চেংমানকে আশ্বস্ত করে বলেন, সময় মতো দাম মিটিয়ে দেওয়ার। এভাবে দেখতে দেখতে এক বছর কেটে যায় মাথা থেকে ছাতির দামের কথা মুছে যায়। কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন ধরে ফেলে মহাজন। মহাজন হিসাব কষে দেখলেন ছাতির দাম চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে হয়েছে হাজার টাকা। ফলে মনমোহন মহাজন চেংমানের থেকে প্রায় একটি হাতির সমমূল্যে ৩৬বিঘা জমি কেড়ে নেয়।
প্রাবন্ধিক বলেছেন ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য না হলেও ডালু -হাজং -গারো জনজাতিরা এর সাক্ষী। আজও সেখানে গেলে এরূপ মহাজনী প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আর এভাবে মহাজনরা দুস্থ সরল প্রজাদের সর্বশান্ত করে।
৮. “আর এক-রকমের প্রথা আছে”– এখানে কোন প্রথার কথা বলা হয়েছে ? কিভাবে সেই প্রথার অবসান ঘটেছিল ?
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছাতির বদলে হাতি নামক প্রবন্ধ এ আমরা মহাজনদের অত্যাচার এর বিভিন্ন রকম কাহিনী জানতে পারি। এই সকল মহাজনেরা যেসব প্রথার তৈরি করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল ‘নানকার প্রথা’।
প্রাচীন বাংলার গ্রামের বিভিন্ন মহাজনরা নিজেদেরকে আরো প্রতিপন্ন করে তোলার জন্য অনেক রকম প্রথা চালু করেছিল। এই সকল প্রথার মাধ্যমে ভূমিহীন চাষিরা চাষ করতে পারলেও উদ্বৃত্ত কিছু ভোগ করতে পারত না। জমিদারের যেসকল চাকর স্বত্ব হীনভাবে জমি ভোগ করতো তাদের বলা হতো নানকার প্রজা। এরা ছিল সাধারণ প্রজাদের থেকে আরও গরিব।
চাষের জমি পেয়ে তারা চাষবাস করতো কিন্তু আসলে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু সময়মতো খাজনা দিতে না পারলে তাদেরকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হতো এমনকি গুদাম ঘরে আটকে রাখা হতো। এই ঘটনার পর নিলাম ডেকে তার বিভিন্ন সম্পত্তির দখল করে নিত জমিদার বা তালুকদারেরা। কিন্তু এই নানকার প্রথা একসময় অবসান ঘটে।
গারো পাহাড়ের উপত্যকায় দুমনাকুরা, ঘোষপাড়া, নওয়াপাড়া, ভুবন কড়া, এসব এলাকায় বসবাসকারী ডালু উপজাতির লোকেরা একজোট হয়েছিল তালুকদার দের বিরুদ্ধে। তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তারা জমির ধান আর জমিদারের খামারে তুলবে না। তারা সিদ্ধান্ত মতো কাজ করতে থাকে। চাষীদের জব্দ করার জন্য থানা পুলিশ হলেও তাতে কাজ হয়নি। এর ফলস্বরূপ জমিদার বা তালুকদারদের একদিন এই নানকার প্রথা তুলে নিতে বাধ্য হতে হয়।
৯. “আর এক-রকমের প্রথা আছে- নানকার প্রথা।” -নানকার প্রজাদের অবস্থা কেমন ছিল ? পরে তাদের অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছিল ? (২০১৫)
উত্তরঃ
নানকার প্রজাদের অবস্থাঃ লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘ছাতির বদলে হাতি’ রচনায় গারাে পাহাড় ও পাহাড়তলির প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে নানকার প্রজাদের কথা পৃথকভাবে আলােচনা করেছেন। জমিদার বা তালুকদারের যেসব প্রজা স্বত্বহীনভাবে চাষজমি ভােগ করত, তারাই ছিল নানকার প্রজা। অন্য প্রজাদের তুলনায় নানকার প্রজাদের অবস্থা ছিল আরও দুর্বিষহ। জমির ফসল বা আম কাঠালে তাদের কোনাে অধিকার ছিল না। জমি জরিপ করার পর তাদের প্রত্যেকের জন্য আড়াই টাকা পর্যন্ত রাজস্ব ধার্য হত। সেই খাজনা দিতে না পারলে তহশিলদার নানকার প্রজাকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে পিছমােড়া করে বেঁধে মারধর করত এবং গুদামঘরে আটকে রাখত। তারপর নিলাম ডেকে সেই প্রজার সমস্ত সম্পত্তি খাসদখল করতেন জমিদার বা তালুকদার। মহাজন প্রজাদের কাছ থেকে ধার বাবদ এক মনের জন্য দ্বিগুণ পরিমাণ ধান আদায় করতেন।
অবস্থার পরিবর্তনঃ গারাে পাহাড়ের নানকার-সহ সমগ্র প্রজা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জেগে ওঠে। এর ফলস্বরূপ তারা তখন জমিদার-মহাজন-পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সােচ্চার হয়। ক্রমশ প্রজারা তাদের অধিকার এবং সম্মান আদায় করতে বিশেষভাবে সক্ষম হয়। পুলিশ বা তথাকথিত ভদ্রলােকরা আর তাই তাদের অসম্মান বা শ্রদ্ধা করতে পারেন না।

কলের কলকাতা
১. “এরা মানুষ না আর কিছু”- কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে ? এমন কথা বলার কারণ কী ?
অথবা,
“লোকটা একজন পয়লা নম্বরের ভন্ড”- কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে ? এমন কথা বলার কারণ কী ?
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘কলের কলকাতা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে জনৈক সরকারি উকিল সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে।
লেখকদের বাড়ি আসতেন একজন সরকারী উকিল। তিনি বাইরের ঘরে বসে লেখকের বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। বাড়ির অন্য কারো সেই ঘরে যাবার অনুমতি ছিল না। লেখক এবং তার দাদা পর্দার আড়াল থেকে সেই উকিলের কথা শুনতেন। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের মামলার গল্প বলতেন, গণেশ ঘোষের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং কল্পনা দত্তের ডায়েরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলতেন। তার কথা শুনে যেকেউ মনে করবে তিনি হয়তো মাস্টারদা সূর্য সেনের দলেরই লোক। বাংলার বিপ্লবীদের বীরত্বের কাহিনী উক্ত উকিলের বলার গুণে লেখকের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।
সরকারি উকিল চলে যাওয়ার পর রাগে লেখকের হাত নিসপিস করত। লেখকের মতে “লোকটা একজন পয়লা নম্বরের ভন্ড”। যতই তিনি বিপ্লবীদের জন্য দরদ দেখান না কেন, তিনি তো একজন সরকারি উকিল এবং ব্রিটিশ সরকারের হয়ে বিপ্লবীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর বন্দোবস্ত তিনিই করে থাকেন। লোকটার প্রতি ক্ষোভে, ঘৃণায় লেখকের মনে প্রশ্ন জাগে- “এরা মানুষ না আর কিছু?”
২. ‘একা আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই’- লেখক কোন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন ? রাস্তায় ঘোরার সময় তার কোন কোন অভিজ্ঞতা হয়েছিল ?
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘কলের কলকাতা’ পরিচ্ছেদে লেখকের কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা বর্নিত হয়েছে। তিনি প্রতিদিন বিকেলে বৌবাজারের মোড় থেকে এসপ্ল্যানেড অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন।
কলকাতা তখন এত জনাকীর্ন ছিল না। রাস্তায় দুপাশে ছিল শুধু ফাঁকা জমি। মঙ্গলা লেনের কাছে চিনাদের থিয়েটার আর আশেপাশে কিছু পাউরুটি কারখানা ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। রাস্তায় রিক্সার উপর বসে ছিল এক সন্যাসিনী বুড়ি। তার সর্বাঙ্গ রূপোর গয়না দিয়ে মোড়া। সে ওড়িয়া ভাষায় অনবরত কীসব বলে যাচ্ছিল আর লোকে ভক্তিভরে তার পায়ে পয়সা দিচ্ছিল।
খালি মাঠে খেলা দেখায় এক জাদুকর। কিন্তু পয়সা দেবার ভয়ে সবাই খেলা শেষ হবার আগেই সরে পড়ে। তখন সেই জাদুকর গালশাপ দিতে শুরু করে।
পাশেই একজন হেকিম হরেকরকম গাছগাছড়া, ছাল চামড়া নিয়ে চিকিৎসার পসার নিয়ে বসেছে। তার দাওয়াইয়ের গন্ধে লেখকের অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসে।
শীতকালে খালি মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ে। সার্কাসের ছেলেরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর বাঘগুলো মানুষের গন্ধে আমোদিত হয়।
হঠাৎ একজন পকেটমার এক ভদ্রলোকের সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অনেকেই তার পিছু ধাওয়া করে কিন্তু চোর ধরা পড়ে না।
লেখক কখনো কখনো চলে যেতেন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর রাস্তায়। সেখানকার পরিবেশ যেমন শান্ত তেমনি দরাজ এখানকার আকাশ। লেখক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিকেলবেলাকার কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। আর একদিন ভালোবেসে ফেললেন নীরস শহর কলকাতাকে।
৩. মোনা ঠাকুরের ‘কলের কলকাতা’ দেখার অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় লেখ।
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘কলের কলকাতা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে মোনা ঠাকুরের কলকাতা দেখার অভিজ্ঞতা বর্নিত হয়েছে। লেখকদের গ্রামেরই ছেলে মোনা ঠাকুর কালীঘাট গিয়েছিল পৈতে নেবার জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে সে তার সমবয়সীদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। মোনা ঠাকুরের অভিজ্ঞতায় কলকাতা শহরের চরিত্র এইরূপ-
আজব শহরঃ মোনা ঠাকুরের মতে কলকাতা এক আজব শহর। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে শুধু গাড়ি আর বাড়ি। হুসহুস করে চলে যায় হাওয়াগাড়ি, রাস্তায় ঠনঠন শব্দে এগিয়ে চলে ট্রাম। কোথাও গ্রামের মতো মাটি নেই-চারিদিকে শুধু চুন, বালি, ইট আর পাথর। কত যে গলি আর কত যে মোড় তার হিসেব নেই এমন আজব শহর কলকাতা।
কলের শহরঃ কলকাতায় কল টিপলে জল পড়ে আর কল টিপলে অন্ধকার দূর হয়ে আলো জ্বলে উঠে। সেখানে রাত যেন দিনের মতো।
আতঙ্কের শহরঃ কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় একধরণের লোক যাদের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে ইয়া ইয়া দাড়ি, হাতে লাঠি আর কাঁধে ঝোলানো থাকত ঝুলি। এরা হল ছেলেধরা। মোনা ঠাকুর একবার এক ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছিল।
খ্যাপা শহরঃ মাঝে মাঝে এই শহরের মাথায় খুন চড়ে যায়। শুরু হয় দাঙ্গা। রাস্তায় রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। প্রাণের ভয়ে মানুষ পালিয়ে যায়। মোনা ঠাকুরও কলকাতা ছেড়েছিল এই দাঙ্গার ভয়ে।
৪. “হঠাৎ একদিন ক্ষেপে উঠল কলের কলকাতা।” ‘কলকাতার ক্ষেপে ওঠা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? কলকাতার ক্ষেপে ওঠার ফল কী হয়েছিল ? ২+৩ (২০১৭)
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘কলের কলকাতা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে লেখক ‘ক্ষেপে ওঠা’ কলকাতার পরিচয় দিয়েছেন।
ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রাণকেন্দ্র। পরাধীনতার বন্ধন মোচন করার জন্য সাধারণ মানুষও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মিটিং, মিছিল, বিদেশি দ্রব্য বিসর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় মিটিং এবং মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্য “জনসমুদ্রে জোয়ার” লেগেছিল। কলকাতার ‘ক্ষেপে ওঠা’ বলতে লেখক এই গণ-অভ্যুত্থানকেই ইঙ্গিত করেছেন।
কলকাতার ক্ষেপে ওঠার ফলে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রায় অনেক প্রভাব পড়েছিল। একইসঙ্গে, ক্ষেপে ওঠা কলকাতা লেখকের জীবনেও অনেক প্রভাব ফেলেছিল। সেগুলি হল যথাক্রমে-
প্রথমতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ারে উত্তাল কলকাতার জনজীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সকলের তখন একটাই লক্ষ- ভারতের স্বাধীনতা। এইজন্য লেখককেও তখন আর ‘বাঙাল’ বলে কেউ খ্যাপানো হত না।
দ্বিতীয়তঃ সকলের মধ্যে বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।
তৃতীয়তঃ কিশোর লেখক পুলিশের তাড়া খেতে খেতে একদিন কলকাতার রাস্তাঘাট চিনে ফেলেছিলেন।
৫. “অমনি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল মা’র কাছে শেখা গান।”- মা’র কাছে শেখা গানটি কী ? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন লেখক ? ১+৪ (২০১৯, ২০২৩)
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘কলের কলকাতা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে কলকাতা নগরীর কাহিনি বিবৃত হয়েছে। লেখক তাঁর মায়ের কাছে যে গানটি শিখেছিলেন সেটি হল- ‘ও তোর শিকল পরা ছল। শিকল পরে শিকলরে তুই করবি রে বিকল’।
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ জোয়ারে তখন সারা কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এমন সময় লেখকদের বাড়িওয়ালা রামদুলালবাবু একবার জেলে গিয়েছিলেন। কদিন পরেই রামদুলালবাবুর দাদা লেখককে রামদুলালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। আনন্দে আটখানা হয়ে লেখক রাজি হয়ে যান। সেই প্রথম লেখকের জেলখানা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা হয়।
ইংরেজদের জেলখানায় মাথা উঁচু করে ঢোকার উপায় ছিল না, সকলকে মাথা হেঁট করে ভিতরে যেতে হত। লেখকও তাই করেছিলেন। জেলখানার ভিতরে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানেই লেখক সুভাষচন্দ্ৰ বসুকে দেখেছিলেন।
জেলখানা থেকে বেরিয়ে লেখক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা ভাবতে শুরু করেন। তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ সরকার তাদেরকে জেলখানার অন্ধকার গুহায় ভরে দিত। লেখক ভাবছিলেন, কী পায় তারা ? অনেক ভেবেও তিনি যখন উত্তর পেলেন না তখন লেখকের ‘মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠেছিল মা’র কাছে শেখা গান।’

মেঘের গায়ে জেলখানা
১. ‘জেলখানায় অসহ্য লাগে অপরাধের তুলনায় শাস্তির এই হেরফের’- কোন জেলখানার কথা বলা হয়েছে ? ‘অপরাধের তুলনায় শাস্তির হেরফের’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন ? ১+৪
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শীর্ষক পরিচ্ছদে উল্লেখিত বক্সার জেলখানার কথা বলা হয়েছে।
বক্সার জেলখানার কয়েদিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক একদল অভিজাত শ্রেণীর কয়েদির কথা বলেছেন। এরা জেলখানার অন্যান্য কয়েদিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা বড় ঘরের, বনেদি বংশের শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’। এদের অপরাধের ধরনটাও একটু অন্য রকমের। যেমন- কেউ নোট জাল করে জেলে গেছে, কেউ ব্যাংকের লাখ লাখ টাকা চুরি করেছে, আবার কেউ খাবারে ভেজাল মিশিয়ে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এরা কেউ তথাকথিত ছোটলোক নয় এবং এদের কাউকে কখনো ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয় নি। এদের মনগুলো এতই নরম যে রক্ত দেখলে অচৈতন্য হয়ে যায়! লেখকের ভাষায়- “তারা সুয়োরানীর ছেলে”। বড়লোক বলেই জেলখানায় এদেরকে শাস্তি পেতে হয়না, বরং জেল কর্তৃপক্ষ এদেরকে সম্মান দেয়, সাধারন কয়েদিরাও এদেরকে সমীহ করে চলে।
অপরদিকে, জেলখানার সাধারণ কয়েদিরা যারা পেটের জ্বালায় পকেটমারি করেছে অথবা জমি হারিয়ে পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করে জেলখানায় গেছে, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। অভিজাত শ্রেণীর কয়েদিদের অপরাধের মাত্রা অনেক বেশি কিন্তু জেলখানায় তারা ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়ায়; আর অন্যান্য কয়েদীরা সামান্য অপরাধ করে চরম শাস্তি ভোগ করে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন “জেলখানায় অসহ্য লাগে অপরাধের তুলনায় শাস্তির এই হেরফের”।
২. ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ রচনা অবলম্বনে বক্সার জেলখানার সাধারণ পরিচয় দাও। ৫
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ পরিচ্ছদে বক্সার জেলখানা যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল-
প্রাকৃতিক পরিবেশঃ এই জেলখানা সম্পর্কে লেখক বলেছেন ‘পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর উপর’ দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে জেলখানাটা যেন ‘মেঘের গায়ে হেলান’ দিয়ে রয়েছে।
জেলখানার গঠনঃ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে দেখা যাবে লোহার ফটক। ফটক পেরিয়ে বাঁদিকে অফিস, কোয়ার্টার এবং সেপাইদের ব্যারাক। তিনটে ফটক পেরিয়ে জেলের অন্দরমহল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাথরের দেওয়াল আর কাঠের ছাদওয়ালা ঘরে থাকে কয়েদিরা। সমস্ত জেলখানাটা কয়েকটি ইয়ার্ডে বিভক্ত। একেকটি ইয়ার্ডে একেকরকমের অপরাধীরা থাকে।
ব্যবস্থাপনাঃ গলায় একটা চাবির রিং ঝুলিয়ে প্রহরারত সেপাই গেটগুলি খুলে খুলে কয়েদিদের ভেতরে ঢোকায় আর বার করে।
কয়েদিদের জীবনযাত্রাঃ জেলখানার প্রাত্যহিক সমস্ত কাজ করতে হয় কয়েদিদের। ‘জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ’ সমস্ত কাজ করেও সামান্য ভুলত্রুটি হলে তাদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন।
৩. “আইনে নেই বলেই টাকা রাখবার মজার কল করেছে তারা”- ‘তারা’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে ? কীভাবে টাকা রাখবার কল বানাতো তারা ? ১+৪
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শীর্ষক পরিচ্ছদে জেলখানার সাধারণ কয়েদিদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশ্নে উদ্ধৃত ‘তারা’ বলতে বক্সার জেলখানার কয়েদিদের কথা বলা হয়েছে।
জেলখানায় নগদ টাকার কারবার হয় না। কয়েদিদের কাছে টাকা রাখাটাই আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু আইনে না থাকলেও কয়েদিরা নগদ টাকার কারবার করে। টাকা দিয়ে তারা নেশার জিনিস কেনে, জেলখানার ভিতরে তাস খেলে, অন্য দলের লোককে নিজের দলে টানে। লেখক বলেছেন, যাদের হাতে পয়সা থাকে জেল তাদের হাতের মুঠোয়। জেলখানার ভেতর প্রভাব বিস্তার করার জন্য টাকার প্রয়োজন অথচ জেলের ভিতর নগদ টাকা রাখা আইনে নেই। এইজন্য কয়েদিরা শরীরের মধ্যেই টাকা রাখার এক বিশেষ রকমের থলি বানাত।
গলার টাকরার কাছে একটা ভারী সীসার বল বেঁধে রাখতে হতো। যত দিন যেত ততই বল ভিতরে ঢুকতো। গলার মাংস ভেদ করে সেই বল যত ভেতরে যেতো ততই দগদগে ঘা হয়ে যেত। একবছর যন্ত্রণা ভোগ করার পর সেই বলটি তুলে নেওয়া হতো। ঘা শুকিয়ে গেলেই থলি প্রস্তুত। সেই গোপন থলিতে সোনা, গিনি যাই রাখা হোক কেউ টের পেতো না। এইভাবেই বক্সার জেলখানার কয়েদিরা টাকা রাখবার মজার কল বানাতো।
৪. “গায়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে- চোট্টা সাধুর ছেলে হবে নির্ঘাৎ বিশে ডাকাত”- সাধু কে ? ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ রচনাংশে সাধুর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো! ১+৪ (২০১৫)
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা সাধুচরণের পরিচয় পাই। সাধুচরণ হলো বক্সার জেলখানার একজন সাধারণ কয়েদি।
সাধুচরণের বাড়ি জয়নগরের কাছে কোন এক আজ গাঁয়ে। তার বয়েস বছর পঞ্চাশ, শরীরে তার মাংস নেই। লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাধুচরণের বেদনাময় জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন।
অনেক কম বয়সেই সাধুচরণ তার বাবা-মাকে হারিয়েছিল। কোনো নিকটাত্মীয় তার দায়িত্বভার নিতে অস্বীকার করে। সেইজন্য পেটের জ্বালায় ছিঁচকে চুরি শুরু করে সে। হাতেনাতে ধরা পড়ে জেলে যেতে হয়েছে তাকে। জেল থেকে বেরিয়ে পাকা সিঁধেল চোর হয়ে উঠেছিল সাধুচরণ। চুরির জন্য বেশ কয়েকবার তাকে জেলেও যেতে হয়েছে। একসময় তার সংসার করবার ইচ্ছা হয়। জমানো টাকা থেকে জমি জায়গা কিনে সংসারে মন দেয় সাধুচরণ।
কিন্তু সে চুরি করা ছেড়ে দিলেও চোরের বদনাম তাকে ছেড়ে যায়নি। আশেপাশের তল্লাটে কোথাও চুরি হলেই পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে যেত। কপালে জুটতো মোটা রুলের গুঁতো। পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচতে নগদ পয়সাও দিতে হতো তাকে। একসময় সাধুচরণেরর মনে হয় যে, চুরি না করে শাস্তি পাওয়ার থেকে চুরি করাই ভালো এবং তারপর আবার পুরোনো জীবনে ফিরে যায় সে।
৫. “জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর ওপর”- কোন জেলখানা ? সেখানে সাধারণ কয়েদিদের ওপর কীরকম অত্যাচার করা হত ? ১+৪=৫ (২০১৮, ২০২২)
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদের আলোচ্য অংশে বক্সার জেলখানার কথা বলা হয়েছে।
লেখক বক্সার জেলের সাধারণ কয়েদিদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরেছেন। সেখানে কয়েদিদের হরেকরকমের কাজ করতে হয়। এরপরও পান থেকে চুন খসলে, অর্থাৎ সামান্যতম ভুল হলে তাদের ওপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। সামান্যতম অপরাধেই জুটে ডান্ডা অথবা লোহার নাল বাঁধানো বুটের লাঠি। এছাড়াও কারো নামে নালিশ এলে তার ডাক পড়ে কেসটেবিলে। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আছে নানারকম শাস্তি। যেমন-
(১) ডিগ্রিবন্ধঃ ছোট ছোট নির্জন কুঠুরিকে বলা হয় ডিগ্রি। কয়েদিদের সেখানে মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়। দরজার নিচে সরু ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা খাবারের থালা ছুড়ে দেওয়া হয়। এ যেন জেলখানার ভেতরে আরেক জেল।
(২) মার্কাকাটাঃ কয়েদিদের প্রতি বছরে তিনমাস করে সাজা মাফ করা হয়। একে বলা হয় মার্কা। জেলের কর্তাদের মন জুগিয়ে চললে মার্কা জোটে নাহলে মার্কা কাটা যায়।
(৩) কম্বলধোলাইঃ সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে মুড়ে আপাদমস্তক লাঠি পেটার শাস্তিকে বলা হয় কম্বলধোলাই।
চোর-ডাকাত-খুনি নিয়ে জেলের কারবার। তাই কয়েদিদের শায়েস্তা করার সবরকম ব্যবস্থাই সেখানে ছিল।
৬. “এরা ছাড়াও জেলখানায় একদল অভিজাত শ্রেণীর কয়েদি আছে”- কাদেরকে ‘অভিজাত শ্রেণীর কয়েদি’ বলা হয়েছে ? তারা অন্য কয়েদিদের থেকে কিভাবে আলাদা ?
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে বক্সার জেলখানার কয়েদিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক একদল অভিজাত শ্রেণীর কয়েদির কথা বলেছেন।
সাধারণ কয়েদিদের থেকে এরা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আর এই ভিন্নতার জন্যই লেখক তাদের অভিজাত শ্রেণীর কয়েদি বা সুয়োরানির ছেলে বলেছেন। সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যগুলি হল-
অপরাধের প্রকৃতিগত: জেলখানার সাধারণ কয়েদিরা অভাবে চোর, অভিজাত শ্রেণীর কয়েদিরা স্বভাবে চোর। তারা কেউ নোট জাল করে জেলে গেছে, কেউ ব্যাংকের লাখ লাখ টাকা চুরি করেছে, আবার কেউ খাবারে ভেজাল মিশিয়ে মানুষ মারার অপরাধে অপরাধী।
অবস্থাগত পার্থক্য: সাধারণ কয়েদিরা অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর কয়েদিরা সকলেই শিক্ষিত এবং বড়লোক তথা বনেদি বংশের ছেলে।
আচরণগত পার্থক্য: সাধারণ কয়েদিদের অপরাধের তুলনায় শাস্তির পরিমাণ অনেক বেশি। জেলখানায় তাদের জন্য নরকবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ, অভিজাত শ্রেণীর কয়েদিদের অপরাধের মাত্রা অনেক বেশি কিন্তু জেলখানায় তারা ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়ায়। শুধু তাই নয়, জেলখানার কর্তাব্যক্তিরাও তাদেরকে আপনি-আজ্ঞে করে এবং সাধারণ কয়েদিরা তাদেরকে সমীহ করে চলে।
৭. “এরা সব সাধুচরণের অতীত”- ‘এরা’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে ? এই প্রসঙ্গে মুস্তাফার পরিচয় দাও।
উত্তরঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে বক্সার জেলে বন্দী একদল কিশোর অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশ্নোদ্ধৃত ‘এরা’ বলতে এই কিশোর কয়েদিদের কথাই বলা হয়েছে।
বক্সার জেলখানার সাত ইয়ার্ডের নিচে শিশু-কিশোর অপরাধীদের থাকার জায়গা। জেলের পরিভাষায় বলা হয় ‘ছোকরা ফাইল’। সেখানেই থাকে মুস্তাফা নামের একটি ছেলে।
মুস্তাফা ভালো পরিবারের ছেলে। তার বাড়ি ছিল এন্টালির কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। তার বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। একদিন কাজ করার সময় উঁচু বাঁশের মাচা থেকে পড়ে তার বাবা প্রাণ হারায়। আচমকাই বদলে যায় তাদের পরিবারের চালচিত্র। মা-ভাইবোন সহ সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্বভার এসে পড়ে মুস্তাফার কাঁধে। এদিকে, পয়সার অভাবে তার পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে যায়।
পাড়াতে থাকত এক পকেটমারের সর্দার। সে মুস্তাফাকে পয়সার লোভ দেখিয়ে পকেটমারের দলে টানে। ধরা পড়ে কয়েকবার তাকে জেলে যেতে হয়েছে। বাস্তব পৃথিবীটা সে অনেক কম বয়সেই দেখে ফেলেছিল। তাই কিশোরসুলভ কোনো ভাবই তার মধ্যে ছিল না।
বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলে মুস্তাফা আজ আর কাউকে কেয়ার করে না। তাই লেখক যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তার ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করে কি না, উত্তরে সে বিজ্ঞের মতো জবাব দেয়- “ইচ্ছে করলেই কি যাওয়া যায়” ?
৮. “মেঘের গায়ে জেলখানা” রচনা অবলম্বনে সাধুচরণ মুস্তাফার জীবনকাহিনি বর্ণনা করাে। ৩+২ (২০২০)
উত্তরঃ
সাধুচরণের পরিচয়ঃ সাধুচরণের বয়স ছিল পঞ্চাশ, গায়ে মাংস ছিল না। তার বাড়ি ছিল জয়নগরের এক গণ্ডগ্রামে। ছােটোবেলা থেকেই পিতৃমাতৃহীন সাধুচরণ আত্মীয়স্বজনের আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য হয়েই খিদের জ্বালায় ছিঁচকে চুরি শুরু করে। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে জেল হয়ে যায় সাধুচরণের। জেল থেকে বেরিয়ে সে পাকা সিঁধেল চোর হয়ে ওঠে। এরপর অনেকবারই তাকে জেলে যেতে হয়। একসময় সে ঠিক করে, অসততার পথ ত্যাগ করে সে সংসার করবে। চোরাই পয়সায় সে কিছু জায়গাজমি কিনে বিয়ে করে। তার এক ছেলেও জন্মায়, নাম বিশে। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি সাধুচরণকে বেশিদিন ভালাে থাকতে দেয় না। গ্রামে চুরি-ডাকাতির কোনাে ঘটনা ঘটলেই থানায় ডাক পড়ে তার। নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে রুলের গুঁতাে খেতে হয়, অনেকক্ষেত্রে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে রেহাই পেতে হয়। তার মনে হয় যে, চুরি করে জেলের ভাত খাওয়া এর চেয়ে অনেক বেশি সুখের। তাই সে আবার ফিরে যায় তার পুরােনাে পেশা চৌর্যবৃত্তিতে। তবে দীর্ঘদিন জেলে থাকায় ছেলে বিশের জন্য আর শুকনাে পড়ে-থাকা চাষের জমির কথা ভেবে তার চিন্তা হত।
মুস্তাফার পরিচয়ঃ মুস্তাফা ছিল বছর দশেকের ফুটফুটে একটি ছেলে। সে জেলখানায় এমন ভাবভঙ্গি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যেন পৃথিবীর কাউকে সে তােয়াক্কা করে না। এন্টালির কোনাে এক স্কুলে-পড়া মুস্তাফার বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রি। হঠাৎ একদিন তিনতলা সমান উঁচু বাঁশের ভারা থেকে পড়ে তিনি মারা গেলে বিধবা মা এবং বেশ কয়েকটি ভাইবােন নিয়ে অথই জলে পড়ে মুস্তাফা। মাইনে দিতে না পারায় স্কুল থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হয়। তাদের বস্তির এক পকেটমার-সর্দার মুস্তাফাকে টাকার লােভ দেখিয়ে তার দলে নিয়ে নেয়। এভাবেই শুরু হয় তার পকেট কাটার পেশা। পকেটমার হিসেবে ধরা পড়ে ইতিপূর্বে সে বারচারেক জেলেও গেছে। ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করে কি না লেখকের এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞের মতাে সে জানায় যে, ‘ইচ্ছে করলেই কি যাওয়া যায় ?’

হাত বাড়াও
১. “সামনাসামনি আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।”— উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনা দিয়ে তাকে দেখে লেখকের অবাক হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করাে।
উত্তরঃ ১৩৫০ বঙ্গাব্দের বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তরের সময়ে সুভাষ মুখােপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের রাজবাড়ির বাজারে ফরিদপুরের গাড়ি আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন।
একটু দূরে স্টেশন-সংলগ্ন মিলিটারি ছাউনির একপাশে একটি অদ্ভুত ধরনের প্রাণীকে দেখে লেখক কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কোনাে চেনা জন্তুর সঙ্গে প্রাণীটির মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে চারপায়ে ভর দিয়ে সে হেঁটে আসতে থাকল।
ভােরের পাতলা কুয়াশা ভেদ করে তার দুটি চোখের তারা যেন জ্বলজ্বল করতে লাগল। সেই চোখের চাউনিতে কেমন যেন একটি অবশ করে দেওয়া মায়াবী শক্তি রয়েছে, এক ঝলক দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। রাস্তা থেকে নানান জিনিস খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল প্রাণীটি।
তার চোখ দুটি কুয়াশায় কী যেন খুঁজে চলেছে। একটু কাছে আসতে দেখা গেল তার সামনের দু-হাতে ঠিক মানুষের হাতের মতােই দুটি থাবা। হাতের আঙুলগুলি লােমহীন, আগার দিকে খানিকটা সরু।
এবার প্রাণীটি মুখােমুখি হতেই বােঝা গেল সে আসলে অমৃতের পুত্র মানুষ, বারাে – তেরাে বছরের একটি ছেলে যার কোমর গিয়েছে ভেঙে, তাই জানােয়ারের মতাে সে চার পায়ে চলে আর রাস্তা থেকে চাল আর ছােলা খুঁটে খায়। মানবতার এইরূপ লাঞ্ছনা লক্ষ করে লেখক বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়েছেন।
২. “তােমরাও হাত বাড়াও, তাকে সাহায্য করাে।”– লেখক কাকে, কীভাবে, কেন সাহায্য করতে বলেছেন ? (২০১৬)
উত্তরঃ সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’ গ্রন্থের শেষ রচনা ‘হাত বাড়াও’ শীর্ষক পাঠ্যাংশে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে বুভুক্ষু বারাে- তেরাে বছরের সম্পূর্ণ উলঙ্গ অনাহারী এক কিশােরকে সাহায্য করার কথা বলেছেন।
লেখক সুভাষ মুখােপাধ্যায় বহুদিনের শাসন- শােষণক্লিষ্ট বাঙালি সমাজকে তথা দেশবাসীকে একে অপরের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক দেখেছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত সেই কিশাের ছেলেটির জ্বলন্ত দুটি চোখ সন্ধান করছে ‘সেইসব খুনি’-দের, যাদের ষড়যন্ত্রে শস্য-শ্যামলা এই বাংলা পরিণত হয়েছে অনাহারের শ্মশানে। তাকে সহানুভূতির স্পর্শ দিয়ে, সংবেদনশীলতার মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। কারণ, অনাহারে ধুকতে ধুকতেও তারা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে।
মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী লেখকের স্পর্শকাতর মন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান সমবেদনা, গড়ে তুলতে চান সচেতনতা। মন্বন্তরের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অসহনীয় সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেন লেখক। তাই তিনি চান বাংলার বুকজোড়া সােনালি ফসলে, চাষির গােলা ভরা ধানে, কারখানায় কোটি কোটি বলিষ্ঠ হাতের কধনমুক্ত আন্দোলনে সুখ-শান্তি ফিরে আসুক এ বাংলায়। সমবেত সাহায্যের হাত যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের অন্ধকার থেকে ‘অমৃতের পুত্র মানুষ’ কে আলোর উৎসে ফিরিয়ে আনুক। এটিই লেখকের একমাত্র কাম্য।
৩. ‘সরু লিকলিকে আঙুল দিয়ে সেইসব খুনীদের সে শনাক্ত করছে’— কে শনাক্ত করছে ? কাদের, কেন খুনী বলা হয়েছে ?
উত্তরঃ উদ্ধৃত অংশটি সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের লেখা ‘আমার বাংলা’ ‘গদ্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘হাত বাড়াও’ রচনা থেকে গৃহীত।
রাজবাড়ির বাজারে বসে লেখক সুভাষ মুখােপাধ্যায় কুয়াশায় মােড়া দুর্ভিক্ষের সকালে যে বারাে – তেরাে বছরের মাজা ভাঙা উলঙ্গ ছেলেটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার ‘ সরু লিকলিকে আঙুলে’র কথা বলা হয়েছে।
শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথের সােনার বাংলা— সেখানে একদিন নেমে এসেছিল প্রকৃতির অভিশাপ। সময়টা ১৩৫০ সন দুর্ভিক্ষের করালছায়া ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘা আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুর শােষণ।
এখানেই শেষ নয়, গ্রামে – গঞ্জে জোতদার, জমিদার, আড়তদার ও কালােবাজারির দল মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তার লেখায় প্রকৃতির নির্মমতার সঙ্গে মানুষের অমানবিক নিষ্ঠুরতার দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
এখানে ‘সেইসব খুনী’ বলতে যাদের শােষণ, লােভ, অত্যাচার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল লেখক তাদের কথা বলেছেন। এরা সাম্রাজ্যবাদী শােষক, গ্রামের জোতদার – জমিদার ও কালােবাজারির দল।
লেখক চান বাংলায় আবার সুদিন ফিরে আসুক, বাংলার মানুষজন সমৃদ্ধ জীবন যাপন করুক। তাই লেখক সেইসব শােষক, খুনি, ষড়যন্ত্র কারীদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এদেরকে সমাজ থেকে নির্বাসন দিতে হবে, তবেই গড়ে উঠবে নতুন সমাজ।
৪. “কিন্তু আজও সেই দুটো জ্বলন্ত চোখ আমাকে থেকে থেকে পাগল করে।”— কার জ্বলন্ত চোখের কথা বলা হয়েছে ? কোন্ ঘটনায় লেখকের এমন উক্তি ?
উত্তরঃ ‘হাত বাড়াও’ রচনাংশে বারাে-তেরাে বছরের একটি উলঙ্গ ছেলের জ্বলন্ত চোখের কথা এখানে বলা হয়েছে।
পাতলা কুয়াশায় মােড়া পাশের দুর্ভিক্ষের এক সকালে লেখক সুভাষ মুখােপাধ্যায় ফরিদপুরের গাড়ির অপেক্ষায় রাজবাড়ির বাজারে বসেছিলেন। সেখানেই বাজার থেকে একটু দূরে স্টেশনের রাস্তায় মিলিটারি ছাউনির পাশে একটি আশ্চর্য রকমের জন্তুকে দেখতে পেলেন লেখক।
ধীরে ধীরে সেটি চারপায়ে এগিয়ে আসে। পরিচিত কোনাে জন্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। কুয়াশার মধ্যেও তার চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন মায়া ছিল, যা লেখকের বুকের রক্ত হিম করে দিয়েছিল। কিছুটা এগিয়ে এসে সেই মূর্তিটা রাস্তার ধুলাে থেকে কিছু খুঁটে খাচ্ছিল।
ঠিক মানুষের হাতের মতাে তার সামনের দুটো থাবা। আঙুলগুলি যেন আগার দিকে একটু বেশি সরু। গায়ে একদম লোম নেই। সেটি সামনা সামনি আসতেই লেখক অবাক হয়ে গেলেন। বারাে-তেরাে বছরের উলঙ্গ একটি ছেলে। কোমর ভেঙে যাওয়ায় সে হাঁটতে পারে না।
তাই জানােয়ারের মতাে চার পায়ে হামাগুড়ি দেয় আর বাজারের রাস্তায় খুঁটে খুঁটে চাল এবং ছােলা খায়। তার সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো লেখককে থেকে থেকে উন্মাদ করে দেয়। আসলে অমৃতের পুত্র মানুষের এইরকম দুর্বিষহ রূপ লেখকের কল্পনাতীত ছিল। তাই তিনি মাঝে মাঝেই সেটি মনে করে চমকে ওঠেন।
আরও পড়ুনঃ
উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাজেশন্ ২০২৪
